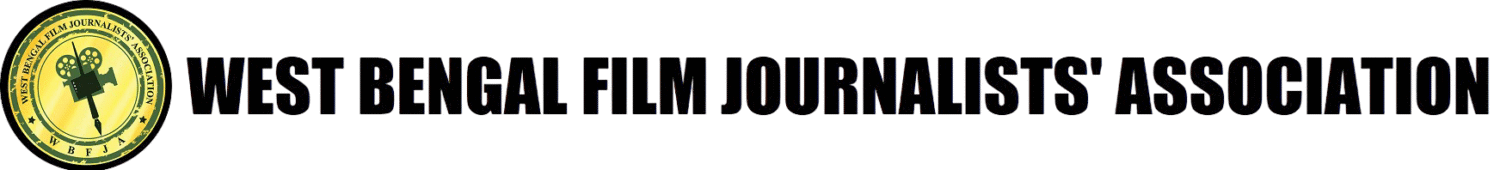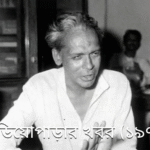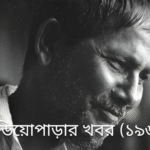ঋত্বিক ঘটক শেষপর্যন্ত বলে গেছেন দেশভাগের, মানুষের লড়াইয়ের কথা
কমলেন্দু সরকার: সত্তর দশকের শুরুতেই একটি সাক্ষাৎকারে ঋত্বিক ঘটক (Ritwik Ghatak) বলেছিলন, “আমি মানুষের জন্যে ছবি করি। মানুষ ছাড়া আর কিছু নেই। সর্ব শিল্পের শেষ কথা হচ্ছে মানুষ। আমি আমার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় সেই মানুষকে ধরবার চেষ্টা করি।” (চিত্রভাষ, জুলাই, ১৯৭০)। এর বছর তিন পর তিনি আর এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, “এই বাংলাদেশ ভাগ হয়ে-যাওয়াটা আমাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক জীবনকে তোলপাড় করে তুলেছিল। সেই সময় আপনাদের বয়স কত ছিল আমি জানি না, তবে তখন জ্ঞানগম্যি যাদের হয়েছিল তাদের জিজ্ঞেস করলে বুঝতে পারবেন, আজকের সমস্ত অর্থনীতি যে চুরমার হয়ে গেছে তার বেসিক ফ্যাক্টর ছিল ঐ বাংলাভাগ।
বাংলাভাগটাকে আমি কিছুতেই গ্রহণ করতে পারি না। আজও পারি না। আর ঐ তিনটে ছবিতে আমি ওকথাই বলতে চেয়েছি। ইচ্ছে না-থাকা হয়ে গেল একটা ট্রিলজি: ‘মেঘে ঢাকা তারা’, ‘কোমল গান্ধার’ আর ‘সুবর্ণরেখা’। আমি ‘মেঘে ঢাকা তারা’ দিয়ে যখন আরম্ভ করলাম তখনও আমি রাজনৈতিক মিলনের কথা বলিনি, এখনও ভাবি না। কারণ ইতিহাসে যা হয়ে গেছে তা পাল্টানো ভীষণ মুশকিল। সেটা আমার কাজও নয়। সাংস্কৃতিক মিলনের পথে যে-বাঁধা যে-ছেদ, যার মধ্যে রাজনীতি অর্থনীতি সবই এসে পড়ে, সেটাই আমাকে প্রচণ্ড ব্যথা দিয়েছিল। আর এই সাংস্কৃতিক মিলনের কথাই ‘কোমল গান্ধার’-এ পরিষ্কার করে বলা আছে, ‘মেঘে ঢাকা তারা’র ভেতরকার কথাও তাই, ‘সুবর্ণরেখা’তেও সেই একই কথা।…” (সিনেমার প্রেমে মশায় আমি পড়িনি, চিত্রবীক্ষণ, অগস্ট-সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩)।
এই দুই সাক্ষাৎকারের বিশেষ কয়েকটি পঙক্তি তুলে ধরলাম তার কারণ তিনি দেশভাগের কথা কোনওদিন ভুলতে পারেননি, ভুলতে পারেননি মানুষের লড়াইয়ের কথা। তাই তাঁর ছবিতে বিদ্যমান দেশভাগ এবং মানুষের লড়াই। আমার ধারণা, তার অন্যতম কারণ, পরিচালক নিমাই ঘোষ-এর ‘ছিন্নমূল’।
আরও পড়ুন: না হতে পারা হিন্দি উত্তম রত্ন
ঋত্বিক ঘটক খুব সামনে থেকে দেখেছিলেন ‘ছিন্নমূল’-এর নির্মাণ। দীর্ঘদিন তাঁকে সময় কাটাতে হয়েছিল ঠাঁইহারা মানুষগুলোর সঙ্গে। ছবিটিতে পরিচালকের সহকারী এবং অভিনেতা হিসেবে কাজ করার সুবাদে। সঙ্গে জড়িয়ে ছিল তাঁর নিজেরও দেশভাগের ক্ষত। সেই ক্ষতের দাগ আজীবন ছিল দগদগে। তাই পরবর্তী সময়ে তিনি যখনই ছবি করেছেন তখন তাঁর ছবির বিষয় হয়ে ওঠে দেশভাগ। পরিষ্কারভাবে বলা যেতে পারে, দেশভাগের পরবর্তী কাল। দেশভাগের ক্ষত নিয়ে ঘোরা মানুষগুলোর কথা, তাঁদের লড়াইয়ের কথা আসে ঋত্বিক ঘটকের ছবিতে। এবং সেসব ভীষণভাবে বাঙালির। যদিও তা অতিক্রম করে হয়ে ওঠে সর্বজনের, সারা বিশ্বের ঠাঁইহারা মানুষের। তাই আজকের সমগ্র চলচ্চিত্রের দুনিয়া ভাবছে ঋত্বিক ঘটকের ছবি নিয়ে। সমগ্র বিশ্বের উদ্বাস্তুদের ছবি হয়ে উঠেছে ঋত্বিক ঘটকের সিনেমা।
বিশ্ববরেণ্য পরিচালক সত্যজিৎ রায় ঋত্বিক ঘটকের স্মরণসভায় বলেছিলেন, “আর একটি কথা বলে আমি শেষ করব— একটা বিশেষ গুণ ঋত্বিকের ছবির। আমরা যারা প্রায় গত চল্লিশ বছর ধরে ছবি দেখেছি, তাদের মধ্যে তো প্রায় ত্রিশটা বছর কেটেছে হলিউডের ছবি দেখে, কেননা কলকাতায় তার বাইরে কিছু দেখবার সুযোগ ছিল না সে সময়টা। উনিশশো ত্রিশ বা পঁচিশ থেকে শুরু করে প্রায় পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বা ষাট অবধি আমরা হলিউডের বাইরে খুব বেশি ছবি দেখতে পারিনি। আমাদের সকলের মধ্যেই তাই কিছু কিছু হলিউডের প্রভাব ঢুকে পড়েছে। কিন্তু ঋত্বিক এক রহস্যময় কারণে সম্পূর্ণ সে প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল; তাঁর মধ্যে হলিউডের কোনও ছাপ নেই। এটা যে কী করে হয়েছে, সেটা এখনও আমার কাছে রহস্য রয়ে গেছে। যদি প্রভাবের কথা বলতে হয়, আমার মনে হয়, ঋত্বিকের ছবিতে কিছুটা— কিছু কিছু সোভিয়েত ছবির প্রভাব লক্ষ করা যায় কিন্তু সে প্রভাবটা— প্রভাব মানে সেখানে অনুকরণ নয়, কারণ ঋত্বিকের প্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁর মৌলিকতা এবং সে সেটা শেষ পর্যন্ত বজায় রেখেছিল। এই সোভিয়েত ছবির প্রভাব এবং সংলাপে, বিষয়বস্তুতে, ছবির পরিসমাপ্তিতে নাটকের প্রভাব তাঁর মধ্যে ছিল। এবং দুটো জিনিস দাঁড়িয়ে ছিল যে ভিত্তির ওপর সেটা একেবারে বাংলার মাটিতে বসানো। ঋত্বিক মনেপ্রাণে বাঙালি পরিচালক ছিল, বাঙালি শিল্পী ছিল— আমার থেকেও অনেক বেশি বাঙালি।” (চিত্রভাষ)
আরও পড়ুন: ‘এতগুলো মালয়ালম ছবি করার পর ভাষাটা রপ্ত হয়ে গিয়েছে’
ঋত্বিক ঘটক এবং তাঁর ছবি এইজন্য বাঙালির এত নিজের, এত কাছের। বিশেষ করে, যাঁরা অল্পবিস্তর দেশভাগের কারণে তার আঁচে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পুড়েছিলেন, পুড়েছেন। স্বাধীনতাকালে তো বটেই বহু মানুষ শিকড়-ছেঁড়া, ভিটে-ছাড়া হয়ে এসেছেন সত্তরের দশকেও। এইসব মানুষেরা যখন পরবর্তী সময়ে প্রেক্ষাগৃহে কিংবা টিভিতে ঋত্বিক ঘটকের ছবি দেখেছেন, বা এখনও দ্যাখেন তাঁদের কাছে মনে হয় এ তো আমাদেরই কথা বলছেন পরিচালক। ‘বলছেন’ এখানেই তিনি অতীত এখনও বর্তমান পরিচালক ঋত্বিক ঘটক। তাঁর কারণ, ভারতের স্বাধীনতার সাতাত্তর বছর কাটলেও, এখনও বহু শিকড়-ছেঁড়া মানুষের ক্ষত শুকোয়নি, হয়তো কোনওদিনও শুকোবে না। ‘নাগরিক’ ছবির মায়ের মতো সর্বদাই স্মৃতিতে আসবে সেই উঠোন, সেই চালতা গাছ, সেইসব পড়শিদের কথা। যাঁদের সঙ্গে আত্মার বন্ধন গড়ে উঠেছিল। বন্ধন ছিঁড়ে গেলেও কোথাও যেন অদৃশ্য একটা সুতোর টান অনুভব করেন মানুষ। দেশ ছেড়ে অন্য দেশে গেলেও। একটা গাছ যেমন উপড়ে নিয়ে অন্য মাটিতে পুঁতলে তেমনভাবে সাড়া দেয় না তেমনই মানুষও এক মাটিতে পালিত হয়ে অন্য মাটিতে এসে মানিয়ে নিলেও সেই পুরনো মাটির গন্ধ লেগে থাকে তাঁর জীবনে। এই মাটির গন্ধ, মানুষের কথা, মানুষের টিকে থাকার লড়াইয়ের কথা বলেছেন ঋত্বিক ঘটক তাঁর ছবিতে। যাঁরা দেশভাগের কারণে জর্জরিত নন, তাঁরাও কোথাও একটা বেদনা অনুভব করেন, তাঁদেরও মনখারাপ করে দেয় ঋত্বিক ঘটকের ছবি, আর শিকড়-ছেঁড়া মানুষেদের ভাবিয়ে তোলে, চোখের জলে আগুন নেভে না তাঁদের বরং ঝিমিয়ে থাকা আগুন আরও একবার জ্বলে উঠে লড়াইয়ের কথা মনে করিয়ে দেয়। দেশভাগ, শিকড়-ছেঁড়া মানুষগুলোকে বোঝা-চেনা, তাঁদের লড়াইকে সামনে এনে দেয় ঋত্বিক ঘটকের সিনেমা। তাই হয়ে ওঠে, হয়ে উঠেছে এক মানবিক ও সর্বজনীন দর্পণ ও দলিল।
আরও পড়ুন: ‘এক ফিল্ম হিরোর কাছ থেকে প্রেমের প্রস্তাব পেয়েছি’
দেশভাগের যন্ত্রণা ঋত্বিক ঘটককে অসম্ভব পীড়া দিয়েছিল এ-কথা নতুন নয়। যদিও এ-কথা না-বললেও ঋত্বিক ঘটক আর ছবি সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাতও করা যায় না। তাঁর প্রতিটি ছবিই দেশভাগের কথা বলে। যে-দেশভাগ নিমাই ঘোষ-এর ‘ছিন্নমূল’ (১৯৫০) বলে, তার পরের প্রসঙ্গ টেনে ছবি করেন ঋত্বিক ঘটক। অর্থাৎ ‘ছিন্নমূল’ ছবি ছিন্নমূল মানুষেরা সীমান্ত পেরিয়ে চলে আসেন অন্য আর এক দেশে। দেশভাগ একরাতেই দেশের একাংশের মানুষকে ভিন্ন করে দেয়। যে-মাটির গন্ধ এত এত বছর নিয়েছিলেন বুকভরে, সেই মাটি অচেনা করে দেয় মুহূর্তেই। চেনা পড়শি অচেনা হয়ে যান, দূরে সরে যান। পাশের যে-বাড়ির মানুষগুলোর সঙ্গে ঈদের দিনে খাবার ভাগাভাগি করেছেন, পৌষপার্বণে পিঠে, পুলি, পাটিসাপটা, পায়েস ভাগ করে খেয়েছেন। তাদের সঙ্গ আর পাওয়া যাবে না। যাওয়ার দিনে চোখের জলে বিদায় নেন নতুন পদযাত্রীরা, বিদায় দেন বহুকালের বন্ধন-ছেঁড়া পড়শিরা। পরিস্থিতি দুই পক্ষকেই কাছাকাছি আর হতে দেয় না, দিল না। দলবেঁধে মানুষ চললেন সীমান্তের দিকে, যে-সীমান্ত দেশভাগ করে দিয়েছে একরাতেই। সেইসব মানুষের কথা বলে নিমাই ঘোষের ‘ছিন্নমূল’। ট্রেন, গরুর গাড়ি, নৌকা ভাসিয়ে মানুষেরা চলে আসেন এদেশে। এক দেশ হল পূর্ব পাকিস্তান আর ভারত। একভাষা, একমানুষ ভিন্ন হল। এখন দুই বাংলার মানুষ সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে বলেন, ওই আমার দেশ ছিল।
হাসান আজিজুল হক-এর ‘আগুন পাখি’র গ্রাম্য বধূটির মতো প্রশ্ন জাগে আজও অনেকেরই মনে, ‘আমাকে কেউ বোঝাইতে পারলে না ক্যানে আলাদা একটো দ্যাশ হয়েছে….এই দ্যাশটা আমার লয়।’ ঋত্বিক ঘটকও ওই গ্রাম্য বধূটির মতো মনে করতেন। উত্তর মেলে না।
আরও পড়ুন: ‘এখনকার ছবি শুক্রবারে আবিষ্কার, সোমবারে পরিষ্কার’
ওই মাটির গন্ধ এখনও পান অনেকেই। কাঁটাতারের বেড়া পেরোনো যায় না। পিঠ রক্তাক্ত হয়। আসলে রক্তাক্ত হয় হৃদয়। যা হয়েছিল পরিচালক ঋত্বিক ঘটকের। যে-রক্তাক্ত হৃদয়ের প্রতিফলন তাঁর ছবি।
আমার ব্যক্তিগত ধারণা, ‘ছিন্নমূল’ ছবিটিই ঋত্বিক ঘটককে দেশভাগের ছবি বানাতে অনেকটাই সাহায্য করে। ঋত্বিক-কন্যা সংহিতা ঘটক তাঁর ‘ঋত্বিক এক নদীর নাম’ বইয়ে লিখছেন, ‘১৯৫১ সালে নিমাই ঘোষ পরিচালিত ‘ছিন্নমূল’ চলচ্চিত্রে আবার সহকারী পরিচালনা ও অভিনেতার চরিত্রে তরুণ ঋত্বিককে দেখা গিয়েছিল। অসম্ভব রোগা মাথায় ভারী ট্রাঙ্ক ইত্যাদি বহন করত, নিয়মিত চিত্রনাট্য বুঝত’।
সংহিতা আবার লিখছেন, ‘১৯৫১ সালেই ‘নাগরিক’ চলচ্চিত্রটির চিত্রনাট্য লিখতে আরম্ভ করে। এদিকে ঋত্বিকের মননে ব্যথা। কোথায় সেই মায়াবী মুহূর্তগুলি। বাংলাদেশে নিজের পিতা ভোরবেলা উঠে পাখি দেখতে বেরুতেন। শহর কলকাতায় তাঁর প্রাণ হাঁপিয়ে উঠত। পায়রা শালিক পাখি দেখতে লাঠি হাতে পথে বেরুতেন ভোরবেলা। ফুল, গাছ, পাখি— কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছিল’। যেমন, ‘নাগরিক’ ছবির রামুর মা প্রভাদেবীর জীবন থেকে বহুকিছু হারিয়ে গেলেও মনে থাকে উঠোনের ধারে সেই চালতা গাছ, পাখি, আরও কিছু। যেসব তিনি ফেলে এসেছেন দেশভাগের কারণে। তিনি অতীত আঁকড়ে থেকেই বাঁচেন। আবার নতুন আস্তানার কথাও ভাবেন। যে-আস্তানা হবে তাঁর ফেলে-আসা বাড়ির মতো।
আরও পড়ুন: ‘অতটা অ্যাপিল করেনি উত্তমকুমারের অভিনয়’
আবার রামুকে বাঁচিয়ে রাখে একটি ক্যালেন্ডার। দেওয়ালে ঝোলানো সেই ক্যালেন্ডারে একটা ছবির ওপর বারবার ক্যামেরা আসে, চলে যায়। ছবিটি অনেকটা ভ্যান গঘ-এর ছবির মতো। যদিও সেটি একটি ফোটোগ্রাফ। বিশাল ধানখেত। উদার খোলা আকাশ। তারই মাঝে লাল টালির একটা বাড়ি। ‘নাগরিক’ ছবিতে দেখি রামু বারবার এসে দাঁড়ান ওই ক্যালেন্ডারের সামনে। তাঁকে বেঁচে থাকার প্রেরণা দেয়। সেই ক্যালেন্ডারের দৃশ্যটির কথা বলেন সবাইকে। ক্যালেন্ডারের ছবিটিই রামুর উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতীক। ঋত্বিক সেই স্বপ্ন ভেঙে দিচ্ছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কড়া গদ্যের মতো। রামু বুঝতে পারেন, যেদিন ভাড়া বাড়ি ছেড়ে যেতে হচ্ছে সস্তার বস্তিতে। তবুও তিনি ভুলে গেলেও ঘরে ঢুকে ক্যালেন্ডারের সামনে দাঁড়ান, দেওয়াল থেকে খুলে মুড়ে নিয়ে চেপে ধরেন। এটা কি ঋত্বিক ইঙ্গিত করলেন, স্বপ্ন ভাঙলেও বিশ্বাসের জোর থেকে যায় মানুষের মধ্যে। লড়াই জারি রাখেন রামুর ভিতর। আসলে, ঋত্বিক ঘটক তাঁর প্রতিটি ছবিতেই ছিন্নমূল মানুষের লড়াইয়ের কথা বলেন, বলেছেনও। সেই লড়াইয়ে হার, জিত অন্য প্রশ্ন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁর লেখার মধ্যে মানুষের লড়াইয়ের কথা বলেন। শুধু মানিক নন, দেশভাগের শিকার যাঁরা সেইসব লেখকদের লেখায় পাওয়া যায় মানুষের বাঁচার লড়াইয়ের কথা। এখানে সেলুলয়েডে গদ্য লেখেন ঋত্বিক। আমরা গ্রোগাসে চোখ দিয়ে পড়ি সেসব।
‘বাড়ি থেকে পালিয়ে’ (১৯৫৯) ছবিতে ঋত্বিক ঘটক অনেক বেশি নির্মম আবার ভালবাসাও বিদ্যমান। অবশ্য সে-ভালবাসা সেই ঠাঁইহারা মানুষটির ভিতর দেখি। শহরের মানুষের কিসের যেন অভাব। শহরের মানুষ জায়গা দিতে চাইছে না বাইরের মানুষকে। যদিও তাঁর ভাষা এক, দেশ এক, যদিও ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত। কাঁটাতারের একদিকে পূর্ব বাংলা অপর দিকে পশ্চিম বাংলা। অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান আর ভারত। দুই দেশের মাঝে একটি কাঁটাতারের বেড়া!
আরও পড়ুন: ‘ছবি পরিচালনার জন্য এখনও প্রস্তুত নই’
‘বাড়ি থেকে পালিয়ে’ (১৯৫৯) ছবিতে ঠাঁইহারা মানুষের কথা এসেছে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে কলকাতা আগত উদ্বাস্তু শিক্ষক এখানে চাকরি পান না। তিনি মনে বলেন, “এই শহরের মাস্টারমশাইদের কোনও দরকার নেই।” তাঁর কাজ হল শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য বহুরূপী সেজে হরিদাসের বুলবুল ভাজা বিক্রি করা। তাঁর প্রকৃত নাম হারিয়ে ‘হরিদাস’ হয়ে উঠেছেন। তারই মাঝে তিনি খুঁজে পান গ্রামের বাড়ি থেকে কলকাতা শহরে পালিয়ে আসা এক উদ্বাস্তু শিশুকে। গ্রামে তার বাড়িঘর থাকলেও শিশুটি কলকাতা শহরে কিন্তু উদ্বাস্তু। এখানে তো তার কেউ নেই। শিশুটির কাছে কলকাতা স্বপ্নের শহর, এল ডোরাডো!
হরিদাস নিজে উদ্বাস্তু হলেও বাচ্চাটিকে ঘরে ফেরাতে চান। সেই কাজে সফল হন হরিদাস। তারপর তিনি কলকাতা শহরের নাগরিকদের মাঝে হারিয়ে যান। হরিদাস জানতেন তাঁর মতো উদ্বাস্তুকে কলকাতা নিজের করে নেয়নি। হয়তো উদ্বাস্তুদের এই শহর নিজের করে নিতে শেখেনি। অন্তত প্রথমদিকে বাস্তবেও এর সত্যতা দেখা গেছিল। এদেশীয়রা পূর্ববঙ্গীয়দের নিজেদের কাছে টেনে নেয়নি সেভাবে। ‘বাঙাল’ বলে ঠাট্টা, মজা করতেও ছাড়তেন না। ওঁদের খাওয়াদাওয়া, সংস্কৃতি ইত্যাদি নিয়ে এখনও কথাবার্তা হয়। এসব নিয়ে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত কৌতুক নকশাও খুব চালু ছিল ষাট থেকে আশির দশকে।
আরও পড়ুন: ‘পচা দুর্গন্ধ ছড়ালে, প্রতিবেশীরাই এসে দাহ করবে’
দেশভাগের যন্ত্রণার কথা ঋত্বিক ঘটক বলেছেন ‘কোমল গান্ধার’ (১৯৬১) ছবিতে পদ্মাপারে দাঁড়িয়ে অনসূয়া আর ভৃগুর কথোপকথনে। অনসূয়া বলছে ভৃগুকে, “কথাটা বোধহয় ‘নিশ্চিন্তি’। আমার ঠাকুমা বলতেন। সেটা বোধহয় আর কোনওদিন ফিরে পাব না। মনে হয়, আমরা কেমন যেন বাইরের লোক হয়ে গেছি। সকালবেলা দেশের কথা মনে পড়ে। নদীর ধারে কত হাঁটতাম। এখানে হাঁটতে পারি না।” একটু থেমে ভৃগুকে বলে অনসূয়া, “চলো, হাঁটবে?” পরিচালক ঋত্বিক ঘটক অনসূয়ার কথার মধ্যে দিয়েই কলকাতার সঙ্গে আগত পূর্ববঙ্গীয়দের সম্পর্কের অবস্থানটা বলে দিলেন। আমার ব্যক্তিগত ধারণা, সেইসময় কলকাতার নাগরিকেরা সম্ভবত ভাবেননি, ওঁরা-আমরা একই, বাঙালি।
ভৃগু বলছে, “ওই পারেই আমার দেশের বাড়ি। ওই যে ঘরগুলো দেখা যাচ্ছে। এত কাছে অথচ কোনওদিন আর পৌঁছতে আর পারব না। ওটা আমার কাছে এখন বিদেশ। ওই যে ট্রেন লাইনটার ওপর আমরা দাঁড়িয়েছিলাম সেখানে কলকাতা থেকে ফেরার সময় আমরা নামতাম। স্টিমার দাঁড়িয়ে থাকত। মা অপেক্ষা করত। আমার একটা মজার কথা মনে হল, রেল লাইনটা ছিল যোগচিহ্ন, এখন হয়ে গেছে বিয়োগচিহ্ন।”
আরও পড়ুন: দীনেন গুপ্তর ছবিতে উত্তমকুমার
আরও দু’চারটে কথার পর দেখা যায় একটি ট্রেন ছুটতে ছুটতে চলে আগের নিশানায়। তারপর ধাক্কা খায় বাফারে। না, আর যাওয়া যায় না। সবশেষ। পর্দাজোড়া অন্ধকার। দেশভাগের কারণে উদ্বাস্তুদের সামনে শুধুই অন্ধকার। সেই অন্ধকার হাতড়ে বাঁচার চেষ্টা। উদ্বাস্তুরা কলোনি তৈরি করেন মাথাগোঁজার জন্য। তেমনই এক জমিদারের ফেলে রাখা পতিত জমি তালপুকুরের ডাঙায় গড়ে ওঠে ‘নবজীবন কলোনি’ ‘সুবর্ণরেখা’য় (১৯৬৫)। নামকরণ হরপ্রসাদের। যিনি উদ্বাস্তু কলোনিতে একটা স্কুল গড়ে তোলেন। ১৯৪৮, জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবসে। কারণ হিসেবে তিনি বলেন, ”শিক্ষায় জাতির মেরুদণ্ড। এসো আমরা সবাই ভারতমন্ত্র উচ্চারণ করি– বন্দেমাতরম।” কলোনির সকলেই সমবেত কণ্ঠে বলে “বন্দেমাতরম।”
ঠিক এই দিন, এই সময়েই জমিদারের লেঠেল বাহিনী এসে হামলা করে ‘নবজীবন উদ্বাস্তু কলোনি’তে। হামলার আগে এক বিধবা বাগদি বউ কলোনিতে আশ্রয় চাইতে আসেন। সেইসময় কলোনির একজন জিজ্ঞাসা করেন, “কোন জেলার?” বিধবা মহিলা বলেন, “ঢাকা জেলার।” তাঁকে পত্রপাঠ বিদায়কালে বলেন ভদ্রলোক, “এখানে হবে না। এখানে সবাই পাবনার। জেলায় জেলায় বিভেদটা যদি জিইয়ে না রাখতে পারি তো কী নিয়ে থাকব! সবই তো গেছে আর কী নিয়ে থাকব!”
আরও পড়ুন: টিন, বাক্স, পেয়ালা, পিরিচ বাজিয়ে এক নতুন ধরণের এক্সপেরিমেন্ট
এটা ‘সুবর্ণরেখা’র এক অন্যতম ভয়ংকর জায়গা। পরিচালক ঋত্বিক ঘটক বাঙালির ঠিক জায়গায় আঘাত করেছেন। আমরা সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বলি আবার ভিতরে ভিতরে ভীষণভাবে সাম্প্রদায়িক। এর সুযোগ নিচ্ছে কিছু স্বার্থান্বেষী। উদ্বাস্তুরা সবকিছু ফেলে এলেও শুধু বিভেদটাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইছেন তাঁরা। আবার মানবিক দিকটাও দেখা যায় অন্যজনের ভিতরে। লেঠেল বাহিনী বাগদি বিধবা বউকে ধরে নিয়ে গেলে তাঁর শিশু পুত্রসন্তানটিকে আশ্রয় দেন কলোনিরই বাসিন্দা-মাস্টার ঈশ্বর চক্রবর্তী। তাঁর শিশুকন্যা সীতা। সীতা যখন হরপ্রসাদকে বলে, “হরপ্রসাদদাদা, তুমি যে গ্রাম ছাড়ার সময় বলেছিলে আমরা নতুন বাড়িতে যাব। এটাই কি আমাদের নতুন বাড়ি?” হরপ্রসাদ ‘হ্যাঁ’ বললে বাচ্চা সীতা প্রশ্ন তোলে, “তাহলে এত মারামারি কেন?” মোক্ষম প্রশ্ন। হরপ্রসাদ বলেন, “ও থেমে যাবে। শান্ত পরিবেশ গড়ে উঠবে। ঈশ্বর তার একমাত্র ছোট বোন সীতার জন্য লড়বে। আমরাও লড়ব।” হরপ্রসাদ জানেন, এ অশান্তি সহজে থামার নয়। এ-লড়াই তাঁদের নিত্যযাপনের অঙ্গ। তাই কলোনির যুবসম্প্রদায়কে পালা করে রাত জাগরণের কথা বলা হয়। সতর্ক করা হয়। বলা হয়, “কলোনির কোনও যুবক ঘুমাবেন না জাগা থাকবেন।” রাতের অন্ধকারে নেপথ্যে ভেসে আসে গোলমালের আওয়াজ। যে-আওয়াজ আমরা শুনেছি সকালবেলা স্কুল উদ্বোধনের সময় জমিদারের লেঠেল বাহিনীর আগমনে। ঋত্বিক ঘটক সীমান্ত পেরিয়ে আসা উদ্বাস্তুদের লড়াইয়ের কথার বলেন তাঁর ছবিতে। তাঁর মনের ভিতর সদাজাগ্রত রেনোয়ার সেই কথা, ‘আমি হলে শুধু দেশভাগের ছবি করতাম।’ ঋত্বিক ঘটক তাই করেছেন। উদ্বাস্তুদের লড়াইয়ের কথা, লড়াইয়ের যাপনচিত্র বারবার এনেছেন তাঁর ছবির বিষয়ে। দেশমাতৃকার কাছে ফিরে না-যেতে পারার যন্ত্রণা কুরে কুরে খেয়েছে ঠাঁইহারাদের। শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া আর কিছুই করে উঠতে পারেননি উদ্বাস্তুরা, পরিচালকও।
‘মেঘে ঢাকা তারা’ (১৯৬০)-র রিতার ‘দাদা আমি বাঁচাতে চাই’ আর ‘সুবর্ণরেখা’র সীতার কণ্ঠে অনুচ্চস্বরে ধ্বনিত হয় ‘দাদা আমি বাঁচতে চেয়েছিলাম।’ ঋত্বিক ঘটকের ছবির প্রতিটি চরিত্রই বাঁচতে চেয়েছিল। লড়াইয়ের মধ্যেও মাথা তুলে দাঁড়াতে চেয়েছে। পেরেছে কি পারিনি পরের কথা। একজন সর্বহারা উদ্বাস্তুর বেঁচে থাকার লড়াইয়ের মধ্যে যে তীব্র আত্মবিশ্বাস, মনের জোর থাকতে হয় তা ঋত্বিক ঘটক জানতেন। তিনি লড়াইটাও জানতেন, লড়াইয়ের স্পৃহাটাও জানতেন, তাই তাঁর ছবির প্রতিটি চরিত্রই প্রচণ্ড আঘাত হানে দর্শকের চিন্তাভাবনায়, হাতুড়ি মারে দর্শকের হৃদয়ে। তাই যতদিন অতিবাহিত হচ্ছে, ততই ঋত্বিক ঘটকের ছবি আরও প্রাসঙ্গিক হচ্ছে।
আরও পড়ুন: উভয় সঙ্কটে রাখি মজুমদার?
ঋত্বিকের ‘নাগরিক’ (১৯৫১ সালে তৈরি হলেও মুক্তি ১৯৭৭-এ) ছবির রামুর মায়ের চরিত্রটি অন্যতম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। তাঁর বারবার মনে পড়া চালতা গাছটির কথা পরিচালক এনেছেন মানুষের হৃদয়ে ঘা-দেওয়ার জন্য। দর্শকদের ভাবাবার জন্যে।
সেইহেতু তিনি যখন বস্তিবাসী তখনও তিনি স্বপ্ন দেখেন চালতা গাছের। স্বপ্ন সফল বা পূরণ না-হলেও কখনও নষ্ট হয় না। তাই তো রামুর মায়ের চিত্রকল্পে ভাসে সেই গ্রাম, সেই চালতা গাছ। কিন্তু ইতিহাসের ফেরে কোনও কিছুই তো আর সম্ভব নয়। না রামুর মায়ের ক্ষেত্রে, না হরিদাসের। কলকাতা তাঁদের আশ্রয় দিয়েছে সেখানেই মানিয়ে নিতে হবে।
আরও পড়ুন: নিষিদ্ধপল্লীতে চোরবেশী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়
ঋত্বিকের প্রায় সব ছবিতেই রয়েছে কলকাতা। থাকারই কথা। কলকাতা তো লড়াইয়ের শহর, আন্দোলনের শহর। তার কারণ, প্রতিটি ছবিই তো দেশভাগের পরবর্তী সময়ের। শিকড়ছিন্ন মানুষের দুঃখ, দুর্দশার কথা। ‘মেঘে ঢাকা তারা’, ‘সুবর্ণরেখা’ কলকাতার প্রান্তে গড়ে উদ্বাস্তু নগর বা কলোনির কথা বলে। শহর কলকাতা আর কলোনি কলকাতা, ইতিহাসের কথা বলে। ভূগোলের কথা বলে, সামাজিক সমস্যার কথা বলে, রাজনীতির কথা বলে, সংকটময় সংস্কৃতির কথা বলে। যা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন গণনাট্য করার সময় এবং পরবর্তী সময়ে। সংস্কৃতির সংকট ঋত্বিক ঘটকের কাছে ভয়ানক এক সমস্যা ছিল। তা দেখি ‘কোমল গান্ধার’ ছবিতে। এই ছবির শুরুতেই নাটকের এক চরিত্র বলে, “কেন যামু দেশ ছাইড়া, যামু ক্যান।” দেশভাগের সঙ্গে এই ছবিতে পাই গণনাট্য আন্দোলন। নাটকের দল গ্রামে যায়। ভোলগার ঢেউ তুফান তুলেছিল গঙ্গাতেও। ষাটের দশকের আগে থেকেই বামপন্থী আন্দোলন জোরদার হচ্ছিল কলকাতাতে। বিশেষ করে, বামপন্থী সাংস্কৃতিক কর্মীদের ভিতর বেশি নাড়া দিয়েছিল। সেখানে দৃষ্টি এড়ায়নি পরিচালকের। ‘কোমল গান্ধার’-এ তার চিত্র অনকটাই পাই। দলের মধ্যে ভাঙন দেখিয়েছেন পরিচালক। যে-ভাঙন তিনি দেখেছিলেন গণনাট্য সঙ্ঘে জড়িত থাকার সময়। আসলে শহরটার ভিতরে মানুষের মধ্যেও ভাঙন ধরছিল সেইসময়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরই সামাজিক, মানসিক ভাঙন ধরেছিল শহরের, মানুষের। পরিচালক বৃহত্তর অর্থে সেই ভাঙনের কথা হয়তো বলতে চান বা চেয়েছিলেন।
আরও পড়ুন: সুপ্রিয়া দেবীর হঠাৎ অবসর, বিপাকে প্রযোজক
রাজনীতির বা রাজনৈতিক সংকটের সঙ্গে সামাজিক সংকট দেখতে পাই ‘যুক্তি তক্কো আর গপ্পো’ ছবিতে।
কলকাতা শহরের ক্যানভাসে সেলুলয়েডে ছবি এঁকেছেন পরিচালক ঋত্বিক ঘটক। সেই ক্যানভাসে যখন বঙ্গবালাকে চিত্রিত করেছেন, তাঁকে দিয়ে বলাচ্ছেন, “বাংলাদেশ থাইক্যা আইছি, এ শহরের পথে পথে ঘুরি, যাওনের জায়গা নাই।” পঞ্চাশের দশকে ঋত্বিক যেমনটি দেখেছিলেন, একই ছবি দেখছেন দুই দশক পরে মাঝ সত্তরে। তখন ছিল পূর্ববঙ্গ, সত্তরে বাংলাদেশ। তখনও ছিন্নমূল, শিকড়ছিন্ন মানুষ আসছেন কলকাতা শহরে। প্রতিটি ছবিই আঁকছেন পরিচালক। পঞ্চাশের দশকে যেমনটি দেখেছিলেন ঋত্বিক তেমনটিই দেখছেন সত্তরে এসে শহর মানিয়ে নিতে পারছে না। ঋত্বিকের ক্ষোভ এখানেই। তাই তো তিনি মানুষের আদিম পেশাকে আনছেন ছবির চরিত্রের মধ্যে। না-খেতে পাওয়া মানুষ দারিদ্রের জন্য আসেন এই পেশায়। ‘নাগরিক’-এর উমার বোন শেফালি এবং ‘সুবর্ণরেখা’র সীতা দু’জনেই দারিদ্রের কারণে বেশ্যা হয়ে যান। সত্যজিৎ রায়ের ‘জনঅরণ্য’ ছবিতে সোমনাথের বোন কণাকেও দেখি একই পেশা নিতে। শহরের এই নিষ্ঠুরতা দেখেছি দুই পরিচালকের ছবিতেই। ‘সুবর্ণরেখা’য় আর একটি ব্যাপার ঘটিয়েছিলেন, যেটি ষাটের দশকে বেশ বৈপ্লবিকই ছিল বাগদি ছেলের সঙ্গে ব্রাহ্মণ মেয়ের প্রেম এবং বিয়ে। শ্রেণি-বৈষম্যকে ভেঙেছিলেন পরিচালক। ষাটের দশকে এটা খুব সহজ কাজ ছিল না কলকাতায়। একুশ শতকের বিশের দশকেও কী খুব সহজ কাজ?
ঋত্বিক ঘটক তাঁর ছবিগুলোতে কলকাতা শহরকে নানাভাবে ধরতে চেয়েছিলেন বা চেয়েছেন। সেখানে কথা এসেছে, এসেছে শব্দ, অন্ধকার দিক, মানুষের লালসা, লোভ ইত্যাদি ইত্যাদি। শব্দের একটা চমৎকার ব্যবহার দেখি ‘কোমল গান্ধার’-এ। অনসূয়া যখন কলকাতা শহরটাকে উপলব্ধি করছে, শহরের টান অনুভব করছে তখনই কানে আসে ট্রামের শব্দ।
আরও পড়ুন: রাজেন তরফদারের পরবর্তী ছবি ‘বনপলাশির পদাবলী’
এখনও প্রতিদিনই উদ্বাস্তুর সংখ্যা বাড়ছে সারা দুনিয়া জুড়ে। ঋত্বিক ঘটকের ছবি যে-উদ্বাস্তু বা ঠাঁইহারা মানুষের কথা বলেছেন তাঁর ছবিতে। একবার জাতিসংঘের রিপোর্টে চোখ বুলিয়ে নিই: ‘As of the end of July 2024, the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) reported that 6.168 million Ukrainian refugees were registered in Europe. This is part of a global total of 6.74 million Ukrainian refugees, with 571,000 living outside of Europe’.
জানা যায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরে ইউরোপে সবচেয়ে বেশি উদ্বাস্তুর সংখ্যা। প্রতি সেকন্ডে নাকি ছ’জন শিশু উদ্বাস্তু হচ্ছে। এ-প্রসঙ্গে সীতার কথা মনে পড়ে যায়। যে-সীতা দাদা ঈশ্বর চক্রবর্তীর হাত ধরে দেশভাগের কারণে উদ্বাস্তু হয়। তাকে বলা হয়েছিল তারা নতুন বাড়িতে যাচ্ছে। পরবর্তী সময়ে উদ্বাস্তু মা সীতা তার পুত্র বিনুকে বলে, তারা একদিন নতুন বাড়িতে যাবে। সীতার আত্মহত্যার কারণে মৃত্যু হলে মামা ঈশ্বর চক্রবর্তীকে বিনু নতুন বাড়ির কথা বলে। কলোনিবাসী সীতা দাদাকে জিজ্ঞেস করেছিল, “এটাই আমাদের নতুন বাড়ি?” দাদা ‘হ্যাঁ’ বললে, সীতা বলে, “তাহলে এত গোলমাল কেন!” বিনুও উদ্বাস্তু কিন্তু পরিস্থিতি পরিবেশ ভিন্ন। সে বলে, “কী মজা, কী মজা।” তাই উদ্বাস্তু শিবিরের পথে শিশুদের দেখার সময় সীতা, বিনু-সহ উদ্বাস্তুদের কথা মনে পড়ে। বিশেষ করে যখন একটি আলোকচিত্রে দেখি ইউক্রেনবাসী এক মা তাঁর দুই শিশুসন্তানকে নিয়ে মাইলের পর মাইল হাঁটতে হাঁটতে চলেছেন উদ্বাস্তু শিবিরের দিকে। ওই দুই উদ্বাস্তু শিশুও হয়তো তাদের মায়ের কাছে জানতে চাইছে নতুন বাড়ি যাওয়ার কথা। ছবি কথা বললেও সে কথা শ্রবণেন্দ্রিয়তে পৌঁছয় না। মনে পড়ে, নিমাই ঘোষের ‘ছিন্নমূল’-সহ ঋত্বিক ঘটকের ছবিগুলি। তাই ঋত্বিক ঘটক আজও অমলিন, ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক। শুধু এদেশে নয়, সারা বিশ্বে।
প্রথম প্রকাশ: জাগ্রত বিবেক
Published by Prabuddha Neogi
আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল ফলো করুন