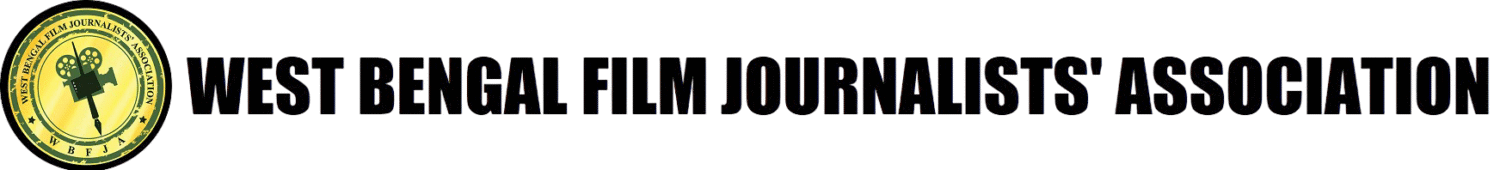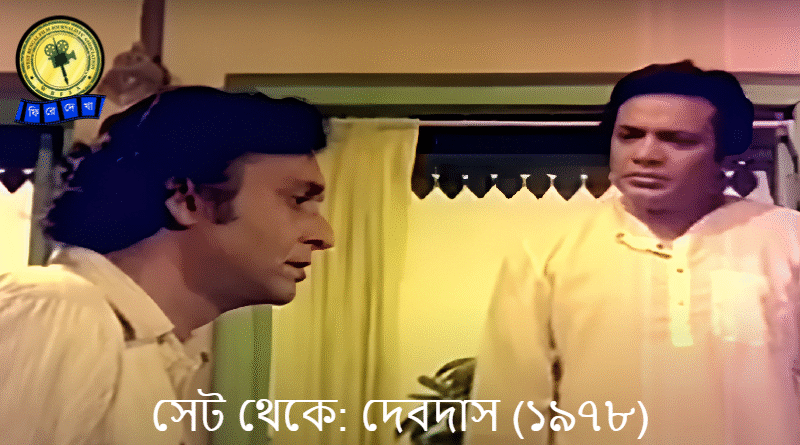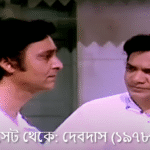সৌমিত্র-উত্তম একসঙ্গে (পর্ব ২)
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় (Soumitra Chatterjee) ও উত্তমকুমার (Uttam Kumar) অভিনীত ছবি ‘দেবদাস’ (Devdas) মুক্তি পেয়েছিল ১৯৭৯ সালে। আজ থেকে ৪৬ বছর আগে সেই ছবির সেটে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক স্বপনকুমার ঘোষ। প্রত্যক্ষ করেছিলেন বাংলার দুই সেরা শিল্পীর অভিনয় নৈপুণ্য। WBFJA-এর পাতায় রইল সেই প্রতিবেদনের অন্তিম পর্ব
প্রথম পর্ব পড়তে এখানে ক্লিক করুন
পরিচালককে জিজ্ঞাসা করলাম, “আপনি ‘দেবদাস’ চলচ্চিত্রায়িত করবার কথা ভাবলেন কেন? বর্তমান সময়ে এ ধরনের বিষয়বস্তুর কোনও মূল্য আছে কি?”
দিলীপ বললেন, “’দেবদাস’ অনেকেই করবেন ভেবেও করেননি, পূর্বের ছবিগুলোর কথা ভেবে। আবার আপনারা, এই ১৯৭৮ সালে, ‘দেবদাস’ চলচ্চিত্রায়ণের কোনও সার্থকতা খুঁজে পান না। কিন্তু একটা কথা আমাকে স্ট্রাইক করেছিল যে, দেবদাস বা দেবদাসেরা এখনও আছে এবং চিরকাল থাকবে। দেবদাস চরিত্রের দোষ বা গুণ হচ্ছে মন, যা অনবরত অস্থির ও চঞ্চল। সে কখনওই জানে না পরের মুহূর্তে কী করবে। এই অস্থিরতা আজকের যুগের ছেলেমেয়েদের মধ্যেও আছে। তার চেহারাটা অবশ্য আলাদা। তাই আমি মনে করি আজকের দিনেও ‘দেবদাস’ অচল বিষয়বস্তু নয়। আমি মূলত অভিনেতা। পরিচালক হিসেবে এমন একটি ছবি আরম্ভ করতে চেয়েছি যাতে প্রথমেই বিতর্কের ঝড় ওঠে। সেটা আজকের গল্প নিয়েও হতে পারত। আবার ৬০ বছর আগেকার গল্প নিয়েও হতে পারত। সবমিলিয়ে দেখুন, ‘দেবদাস’ রীতিমতো আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার ‘দেবদাস’-এর প্রতি আকর্ষণ, দেবদাসের ভিতরে যে জ্বালা আছে, তা আজকের মতো করে বলার প্রয়োজন আছে বলে। আগে যতবার ‘দেবদাস’ হয়েছে, আমার মনে হয়েছে জ্বালার ব্যাপারটা তাতে তেমনভাবে প্রকট ছিল না। আমি সেই জায়গাটা ধরবার চেষ্টা করছি যেখানে একটা পলাতক মন, অস্থির মন, বাউল মন তাকে সর্বদা তাড়া করে নিয়ে চলেছে।”
‘দেবদাস’ কি কমার্শিয়াল সাকসেসের কথা ভেবেই করছেন?
“প্রথম ছবি করছি, স্বাভাবিকভাবেই কমার্শিয়াল সাকসেসের দিকে ঝোঁক তো থাকবেই। আর আজকের চলচ্চিত্র ব্যবসায় সঙ্কটের কথা সকলেই জানেন। এ সময় ছবিকে কতদূর কমার্শিয়ালি সাকসেসফুল করা যায়, সেটা আগে ভাবা দরকার। সেই কারণেই উত্তম-সৌমিত্র (Uttam-Soumitra) জুটিকে ফিরিয়ে আনা। যে করেই হোক বাংলা ছবিকে বাঁচাতে হবে। আমি বলছি না যে চলা উচিত নয় এমন ছবি চলুক। তাতে বরং বাংলা ছবির অপমৃত্যু ঘটবে। এমন ছবি চলুক যাতে মানুষের সুখ-দুঃখ, জ্বালা-যন্ত্রণা, আনন্দ-বেদনা নিয়ে একটা নিটোল জীবনের ছবি আছে।”
বর্তমানে ‘দেবদাস’কে আপনি কীভাবে তুলে ধরছেন? অর্থাৎ বিষয়বস্তুকে কীভাবে ট্রিট করছেন?
“কতগুলো জায়গা বললে বোঝা যাবে আমি বিষয়বস্তুকে কীভাবে ট্রিট করছি। একেবারে শেষের দিকে আসি, যখন পার্বতীর কাছে খবর পৌঁছল দেবদাস গাছতলায় পড়ে আছে। পার্বতী দৌড়ল দেবদাসের কাছে যাওয়ার জন্য। এখানে শরৎচন্দ্র লিখেছেন, ‘ভুবন চৌধুরী চিৎকার করিয়া উঠিলেন, তোরা কি সব ক্ষেপে গেলি? ধর-ধর ধরে আন ওকে। পাগল হয়েছে। ও মহেন, ও কনে বউ। তাহার পর দাসী-চাকর মিলিয়া ধরাধরি করিয়া পার্বতীর মুর্চ্ছিত দেহ টানিয়া আনিয়া বাটীর ভিতর লইয়া গেল।’ তার মানে জমিদারবাড়ির চৌহদ্দি পার্বতী পেরোতে পারল না। তার আগেই মুর্ছা গেল। আমার মনে হয়েছে শরৎবাবু বলতে চেয়েছেন, এই সমাজের বিধি-নিষেধের গণ্ডির বাইরে যাওয়ার ক্ষমতা পার্বতীর ছিল না। বা তাকে যেতে দেওয়া হলো না। আমার ছবিতে আমি দেখাচ্ছি এইভাবে, পার্বতী দৌড়ে গেল। জমিদারবাড়ির সিংহদুয়ারের কাছে যখন পৌঁছল তখন ভুবন সামনের বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। তার গায়ের চাদরটা খুলে পড়েছে। আদেশের সুরে ‘পার্বতী’ বলে ডাকল। সঙ্গেসঙ্গে পার্বতী ‘দেবদা’ বলে ডাকল। ওখানেই আমি পার্বতীকে ফ্রিজ় করে দিচ্ছি। সে এই গম্ভীর আদেশের বাইরে যেতে পারল না। আটকে গেল অনন্তকালের জন্য।
শরৎচন্দ্র এরপর লিখেছেন, ‘এখন এতদিনে পার্বতীর কি হইয়াছে? কেমন আছে জানি না, সংবাদ লইতেও ইচ্ছা করে না।’ এই লাইনগুলো আমি কমেন্টারিতে রাখছি। এবং ওই ফ্রিজ় হওয়া পার্বতীর চেহারাটা ক্রমশ আউট-অফ-ফোকাস হতে থাকবে। যখন একেবারে ঝাপসা হয়ে যাবে তখন ক্যামেরা ফোকাস করবে দেবদাসের ওপর, যেখানে ও শুয়ে আছে। দেবদাসের ওপর কতগুলো শুকনো পাতা পড়ে আছে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে। যেমন, সেই সময়কার সামাজিক অবস্থাটা বোঝাবার জন্য উক্ত ঘটনার আগে দেবদাসকে যখন শুইয়ে দিয়েছে গাড়োয়ান, তার পরের দিন সেখানে লোকের ভিড়। তার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকবে একজন বৃদ্ধ। তার হাত ধরে দাঁড়িয়ে থাকবে একটি ছোট্ট ছেলে। দেবদাসের জামাটা একটু সরে যেতে পারে। পৈতেও দেখা যেতে পারে। দেবদাস অসুস্থ অবস্থায় শুয়ে থাকবে, জল চাইবে। সেইসময় ছোট্ট ছেলেটির মনে হওয়া স্বাভাবিক, অসুস্থকে জল দেওয়া উচিত। সে দাদুর হাত টেনে বলবে, ‘দাদু, জল চাইছে।’ দাদু বলবে, ‘শুনেছি।’ সে বলবে, ‘জল নিয়ে আসি।’ দাদু বলবে, ‘না। দেখছ না ব্রাহ্মণ।’ যারা সেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সকলে অব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ মারা যাচ্ছে, কিন্তু তাকে জল দেওয়া যাবে না। এই ঘটনাটার দ্বারা বোঝানো যাবে সেই সময়ের সামাজিক পরিবেশ, পরিস্থিতি, মানসিকতা, জাত, বিচার।”
কিছু-কিছু জায়গায় তো আপিন মূল উপন্যাস থেকে বাইরে এসেছেন।
“বাইরে আসতে হয়েছে তার কারণ, কিছু-কিছু চরিত্র আমার মনে হয়েছে অপরিস্ফুট থেকে গিয়েছে। যেমন দেবদাসের বাবার চরিত্র। শরৎচন্দ্র লিখেছেন, দেবদাসের বাবা দেবদাসকে এক জায়গায় বলছেন, ‘তুমি আমাকে চিরদিন জ্বালাতন করিয়াছ, যতদিন বাঁচিব ততদিন জ্বালাতন হইতে হইবে।’ এই যে মেজাজটা, তাকে যদি পরিপূর্ণ রূপ দিতে হয়, তার ব্যক্তিত্বকে ফোটাতে হয়, তার জন্য প্রস্তুতি প্রয়োজন। তাই আমাকে একটা নতুন দৃশ্য জুড়তে হয়েছে পার্বতীর বিয়ে প্রসঙ্গে, যা উপন্যাসে নেই। যেমন চুনিলাল। পূর্বের ছবিগুলোতে দেখানো হয়েছে চুনিলাল স্বার্থপর এবং আত্মকেন্দ্রিক, যে নিজের ভালো ছাড়া কিছু বোঝে না। দেবদাস জমিদারের ছেলে, সেইজন্য তাকে যদি চন্দ্রমুখীর কাছে নিয়ে যাওয়া যায়, তবে তার ঘাড়ে বন্দুক রেখে চুনিলালের কিছু সুবিধে হয়।”
কিন্তু উপন্যাসে চুনিলালের চরিত্রের যে সুর পেয়েছি তাতে কিন্তু পূর্বের চরিত্ররূপ মেলে না।
“আমি চুনিলালকে একটা চরিত্র করে তুলেছি, যার মধ্যে ব্যথাও আছে, যন্ত্রণাও আছে। যেমন চন্দ্রমুখী ও পার্বতীকে এক জায়গায় দেখা করিয়েছি, যা উপন্যাসে এবং পূর্বের ছবিগুলোতে নেই। আর একটা কথা চালু আছে। কেউ মদ খেলেই বলা হয়, কি রে, দেবদাস হলি নাকি? আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি কিছু ভোলার জন্য মদ খাওয়া অজুহাত মাত্র। আমার ছবিতে দেবদাস তাই বলেছে, সে মদ খায় মদ খাওয়ার জন্য, কোনও কিছু ভোলার জন্য নয়। যারা বলে মদ খায় দুঃখ-কষ্ট ভোলার জন্য, তারা নিজেদের ঠকায়, শঠতা করে।”
আজকের চলচ্চিত্রের অভিনয়রীতি অনুযায়ী, উপন্যাসের নাটকীয় পরিস্থিতিগুলোকে আপনি কতদূর অনাটকীয় করেছেন?
“না, সেটা করছি না। এমন একটা বিষয়বস্তু নিয়ে ছবি করছি যা অনাটকীয় করার কোনও সুযোগ নেই। আমি মনে করি, যুক্তি নেই। অনাটকীয় ছবি করার জন্য অন্য বিষয়বস্তু আছে। এটা সেই বিষয়বস্তু নয়। এখানে আজকের চলচ্চিত্রের ভাষা ব্যবহার করলেও নাটকীয় পরিস্থিতিকে যতদূর সম্ভব নাটকীয় করেই তুলতে হচ্ছে। আমি আজকের পরিচালক। তার মানে এই নয় উপন্যাসের মূল সুরকে নষ্ট করে আজকের ছবি তৈরি করব। যদি কখনও করি তবে অনাটকীয় ফর্ম অনুযায়ী সেরকম বিষয়বস্তু নিয়ে ছবি করব।”
পরিচালক হিসেবে আপনি আপনার ছবি তৈরি করার উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু বলবেন কি?
“আমি সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে একেবারে অপূর্ণ রেখে ছবি তৈরি করতে চাই না। আমি ছবি তৈরি করতে এসেছি সাধারণ মানুষের জন্য। সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, জ্বালা, যন্ত্রণা, আনন্দ, বেদনা নিয়ে জীবনের ছবি, সেলুলয়েডে তুলে ধরতে চাই।”
(সমাপ্ত)
প্রথম প্রকাশ: আনন্দলোক, সেপ্টেম্বর ১৯৭৮
Edited by Balmiki Chatterjee
Published by Prabuddha Neogi
আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল ফলো করুন