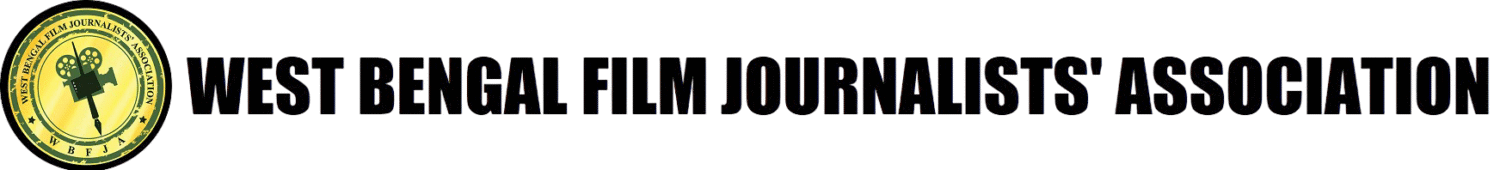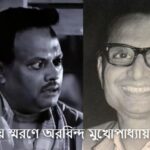শেষ নাহি যে
বাল্মীকি চট্টোপাধ্যায়: আচ্ছা, না হয় ধরেই নিলাম ঋতুপর্ণ ঘোষ (Rituparno Ghosh) বড় পরিচালক। তাঁর ছবি কালজয়ী হবে কি? মানে, আগামী পঁচিশ বছর পর ওঁর ছবি লোকে দেখবে? দেখলে কোন ছবি দেখবে? বা ক’টা ছবি মনে রাখবে!
প্রশ্নগুলো মনে হচ্ছিল বহুদিন থেকেই। এদিকে ঋতুপর্ণর সঙ্গে কাজের সূত্রে দীর্ঘদিনের মেলামেশা। ফলে ওঁর কাজ, ব্যক্তিত্ব, চালচলনের সঙ্গে সম্যক পরিচিত। যা হয়, একজন মানুষের সান্নিধ্যে থাকলে ছোটখাট দোষত্রুটি চোখ এড়িয়ে যায়। তেমনই ওঁর ঔদ্ধত্য দেখে মনে হতো, পায়ের তলায় সান বাঁধানো মেঝে পেলে এমনই হয়। এতে অন্যায় কোথায়! ওঁর অহঙ্কার দেখলে বোধ হতো, বড়াই করার মতো অলঙ্কার থাকলে তা তো করাই যায়! ওঁর ছবির বিষয় দেখে প্রশ্ন জাগত, এটা কী নেহাত ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার ছবি হল না?
উত্তরও তৎক্ষণাৎ সাজিয়ে নিতাম, হতেই পারে। পঞ্চকোষে আবৃত এক স্রষ্টা। তাঁর অন্তর্নিহিত স্ফুলিঙ্গ তো শরীর ফুঁড়ে বেরোতেই পারে!
আরও পড়ুন: ‘এক ফিল্ম হিরোর কাছ থেকে প্রেমের প্রস্তাব পেয়েছি’
উত্তর আজও পাইনি। খোঁজে আছি, ঋতুপর্ণর মৃত্যুর তেরো বছর পরেও। অনুভব করেছি, একটা অদম্য শক্তি, এনার্জির আধার ছিল ঋতুপর্ণ। শরীর পুরুষের, মন নারীর। ভেতরে-ভেতরে এই দুই স্বত্ত্বার দ্বন্দ্ব চলত প্রতিনিয়ত। শুম্ভ নিশুম্ভ যুদ্ধ। সেখান থেকে বেরোতে গেলে একটা প্রবল শব্দ হয়। শেকল ছিঁড়ে বেরোবার সময় যেমন ঝনঝনানি শোনা যায়!
বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে বরাবরই চলচ্চিত্র-শিক্ষিত পরিচালকদের সংখ্যা কম। প্রত্যক্ষজ্ঞানী পরোক্ষজ্ঞানীদের, মানে, দেখে শেখা আর ঠেকে শেখা পরিচালক বেশি। সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেনের উত্তরাধিকার বর্তেছিল তরুণ মজুমদার, তপন সিংহ, সামান্য কয়েকটা ছবি করলেও রাজেন তরফদার, তারপর অপর্ণা সেন, গৌতম ঘোষ, বুদ্ধদেব দাশগুপ্তদের ওপর। সেই মশাল এসে পড়ল ঋতুপর্ণর হাতে। ঋতুপর্ণ বলিয়ে কইয়ে, ইংরেজি ও বাংলায় সমান পারদর্শী। দুর্ধর্ষ লেখেন, বলেন। বিজ্ঞাপণ সংস্থায় কাজ করতেন, তাই চটকদার লাইন করায়ত্ব। বাবা-মায়ের নেওটা ছিলেন বলে রামায়ণ-মহাভারত আত্মস্থ। বাড়িতে একটা ফিল্মি আবহাওয়া তিরতির করে বইত, বাবা সুনীল ঘোষের কারণে। তিনি তথ্যচিত্র নির্মাতা ছিলেন। মানে, সলতে পাকানোই ছিল। ঘি ঢেলে জ্বালানো যা বাকি।
আরও পড়ুন: ‘ছবি পরিচালনার জন্য এখনও প্রস্তুত নই’
এর সঙ্গে যোগ হয়েছিল ঋতুপর্ণর লেখার হাত আর হাতের লেখা। দুটোই অসাধারণ। হঠাৎ করে চোখে পড়ার মতো। আর একটা জিনিস প্রথম দিকে ঋতুপর্ণকে সাহায্য করেছিল তা হল ওঁর আদুরে ভাব। যে কারণে প্রথমেই মানুষের ভালবাসারজন হয়ে পড়তেন। যেমন পড়েছিলেন জয়া বচ্চনের। অপর্ণা সেনের। ঋতুর প্রথম ছবি ‘হীরের আংটি’। হলে মুক্তি না পেলেও, প্রথম ছবিতেই বুঝিয়ে দিলেন আগামী কয়েক দশক বাংলা বিজয়ের সব অস্ত্র মজুত তাঁর কাছে।
ঋতুপর্ণ যদি সিনেমা না করে বিজ্ঞাপনেই কাজ করতেন, নাম করতেন। ঋতুপর্ণ যদি ফিল্ম ডিরেক্টর না হয়ে সাহিত্যিক হতেন, নাম করতেন। ঋতু যদি টিভি সঞ্চালক হতেন, তাতেও নাম করতেন। নাম করার অনেকগুলো গুণ ওঁর হাতে লেখা ছিল। এমনকী ঋতুপর্ণ যদি বুদ্ধিবিক্রেতা হতেন, নাম করতেন।
আরও পড়ুন: ‘অতটা অ্যাপিল করেনি উত্তমকুমারের অভিনয়’
আর যেটা জানতেন না, তার ধারেকাছে ঘেঁসতেন না। এটাও নাম বজায় রাখার একটা লক্ষ্ণণ। ঋতুর জীবনের শেষ কয়েকটা বছর রাজ্য রাজনীতিতে ঝড় বয়ে যাচ্ছিল। চৌত্রিশ বছরের একটা পাকাপোক্ত সরকার নড়বড় করছে। নট নটীরা সেই ঝড়ে গা ভাসিয়ে বুদ্ধি খাটিয়ে আগামী কয়েক বছরের জন্য নিশ্চিন্ত কোটর খুঁজে নিচ্ছেন। ঋতুপর্ণ তখন বাড়াবাড়ি রকমের সেলেব্রিটি। গণ্ডাখানেক জাতীয়, আন্তর্জাতিক পুরষ্কার তাঁর ঝুলিতে। টিভি শোতে টিআরপি উঁচুর দিকে। একটি ম্যাগাজ়িনের সম্পাদক। বিভিন্ন বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু তিনি। নিত্যদিনই তাঁর ছবি, চালচলন, পোশাক নিয়ে কোনও না কোনও কাগজে লেখালেখি হচ্ছে। মুম্বইয়ের তারকারা তাঁর ছবি করার জন্য এক পায়ে খাঁড়া। ফলে খুব স্বাভাবিক ভাবেই রাজনৈতিক দল আড়ালে আবডালে প্রতিনিধি পাঠাতে শুরু করেছে। এ মিটিংয়ে ডাকছে তো তাই শুনে অন্যজনও দেখা করতে চাইছে!

অনন্যা চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে
ঋতুপর্ণ এই রাজনীতির ঘাঁতঘোঁতগুলো বুঝতেন না। যেমন আয়ত্বে ছিল না হিন্দি। তাই অফার থাকলেও মুম্বইয়ে গিয়ে কাজ করেননি। শাহরুখ খান (Shah Rukh Khan) বারবার করে চেয়েছিলেন তাঁকে নিয়ে ছবি করার জন্য। ঋতু রাজি হননি। তেমনই রাজনীতির থেকেও গা বাঁচিয়ে চলেছিলেন। বা বলা যেতে পারে এড়িয়ে গিয়েছিলেন। আঁচ করেছিলেন, ওই রাস্তায় গিয়ে কেবল হোঁচটই খেতে হবে। আখেরে কাজের কাজ হবে না। ঋতু অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিলেন।
চিলড্রেনস ফিল্ম ডিভিশনের ছবি ‘হীরের আংটি’। জয়া বচ্চন তখন সেই কমিটির চেয়ারম্যান। স্ক্রিপ্ট নিয়ে দু’চারদিন আলাপ আলোচনার পরেই জয়া বচ্চন হয়ে গেলেন জয়াদি। ঋতুপর্ণ সটান চলে গেলেন জুহুর জলসা বাংলোতে। দারোয়ান কিছুতেই ঢুকতে দেবে না। ঋতু ঢুকবেই। শেষ পর্যন্ত ঢুকলেন। বসলেন। জয় করলেন। অমিতাভ বচ্চনকে অমিতদা বানিয়ে বেরিয়ে এলেন। ওই ছবির জন্য ঋতু মুম্বই থেকে নিয়ে এসেছিলেন ক্যামেরাম্যান রঞ্জন পালিতকে। শুটিং শুরু হওয়ার কিছুদিনের মধ্যে কী একটা সমস্যা হওয়ার জন্য রঞ্জন আর কাজ করলেন না। সেই জায়গায় এলেন গিরিশ পাধিয়ার। তারপরের একুশ বছরে এসেছেন অভীক মুখোপাধ্যায, শমিক হালদার, গোপি ভগত, হরি নায়ার, বিবেক শাহ। ক্যামেরার কাজ নিয়ে উচ্চ প্রশংসা হয়েছে। ঋতুপর্ণ কোনওদিন ক্যামেরার ব্যাপারে বেশি মাথা ঘামাননি। ভিডিয়ো অ্যাসিস্ট আসার আগে ক্যামেরায় লুক থ্রু করেছেন ওই মাঝেসাঝে। নিয়মিত নয়। কী চাই, কোন সিন, কে শিল্পী, দৃশ্যের আগে পরে কী ছিল বলেই দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছেন সিনেমাটোগ্রাফারের ওপর। সেই ফাঁকে ঋতু ভরিয়ে ফেলতেন সেটের আনাচকানাচ। সেটের যে অঞ্চল ক্যামেরার পিছনে থাকবে, সেই জায়গাও ছাড় পেত না। সারা বছর গোটা কলকাতা শহর ঘুরে খুচখাচ জিনিস সংগ্রহ করাটা ছিল ঋতুর নেশা। মাথার মধ্যে সব সময় কোনও না কোনও ছবির প্লট খেলে বেড়াত। তার সঙ্গেই আসত চরিত্র, তার হাত ধরে থাকত কস্টিউম আর প্রপস।
আরও পড়ুন: ‘এখনকার ছবি শুক্রবারে আবিষ্কার, সোমবারে পরিষ্কার’
সত্যজিৎ রায় খুব ডিটেলিংয়ে নজর দিতেন। হাওয়ায় দেওয়ালের ক্যালেন্ডার নড়ে। তাই একটা অর্ধচন্দ্রাকৃতি দাগ হয়ে যায়। ক্যালেন্ডার সরালে সেই দাগ দেখা যায়। চোখ এড়াত না সত্যজিতের। ঋতুপর্ণর ‘দ্য লাস্ট লিয়র’-এ অমিতাভের নাকে চশমার দাগ, মানে নোজ় ব্রিজ আঁকার জন্য মেকআপম্যানকে একঘণ্টা ঘাম ঝরাতে হয়েছিল। অমিতাভ বচ্চনও গভীর ধৈর্য নিয়ে নাক পেতে বসে থেকেছেন। ছবির বৈভবের মধ্যে সেই নাক-সেতু হারিয়ে গিয়েছে! প্রপস, সেট সাজানো, কস্টিউম, অত্যন্ত সূক্ষ্ণ খুঁটিনাটি বিষয়গুলো আস্তে-আস্তে ঘাড়ে চেপে বসেছিল ঋতুপর্ণর। ছবির উৎকর্ষ নিয়ে ভাবার থেকে এগুলোতে সময় ব্যয় করতেন বেশি। সেই কারণে ছবির বিষয়, চিত্রনাট্য, সেট, প্রপস, কস্টিউম থাকত তাঁর দায়িত্বে। ছবিটা হয়ে যেত ক্যামেরাম্যানের।
তাতে কিছু আসে যায় না। বহু পরিচালক ক্যামেরা বুঝতেন না। প্রখ্যাত পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়কে যখনই তাঁর ক্যামেরাম্যান জিজ্ঞাসা করতেন, ‘দাদা ক্যামেরা কোথায় বসাব?’ অরবিন্দবাবু বলতেন, ‘একটা পরিস্কার জায়গা দেখে বসিয়ে দাও না।’ তাতে অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের ছবির বক্স অফিসের কোনও হেলদোল হয়নি। বেশিরভাগ ছবিই রমরম করে চলেছে। এখনও টিভিতে ‘ধন্যি মেয়ে’ দিলে লোকে হামলে পড়ে দেখে। কিন্তু অরবিন্দবাবুর ছবি কখনও ‘সংসার সীমান্তে’ হয়নি, ‘পলাতক’ হয়নি, ‘হারমোনিয়ম’ হয়নি। ‘সাগিনা মাহাতো’, ‘হাটে বাজারে’, ‘গল্প হলেও সত্যি’ হয়নি। সত্যজিৎ, মৃণাল, ঋত্বিক ছেড়েই দিলাম। তাহলে কী ওই ধরণের ছবি ছাড়া আর কোনও ছবি, ছবি নয়! কখনওই তা নয়। শুধু কালজয়ী হয়ে উঠতে পারেনি। এই লেখার বিষযটা সেটাই ছিল। ঋতুপর্ণর ছবি কি কালজয়ী!
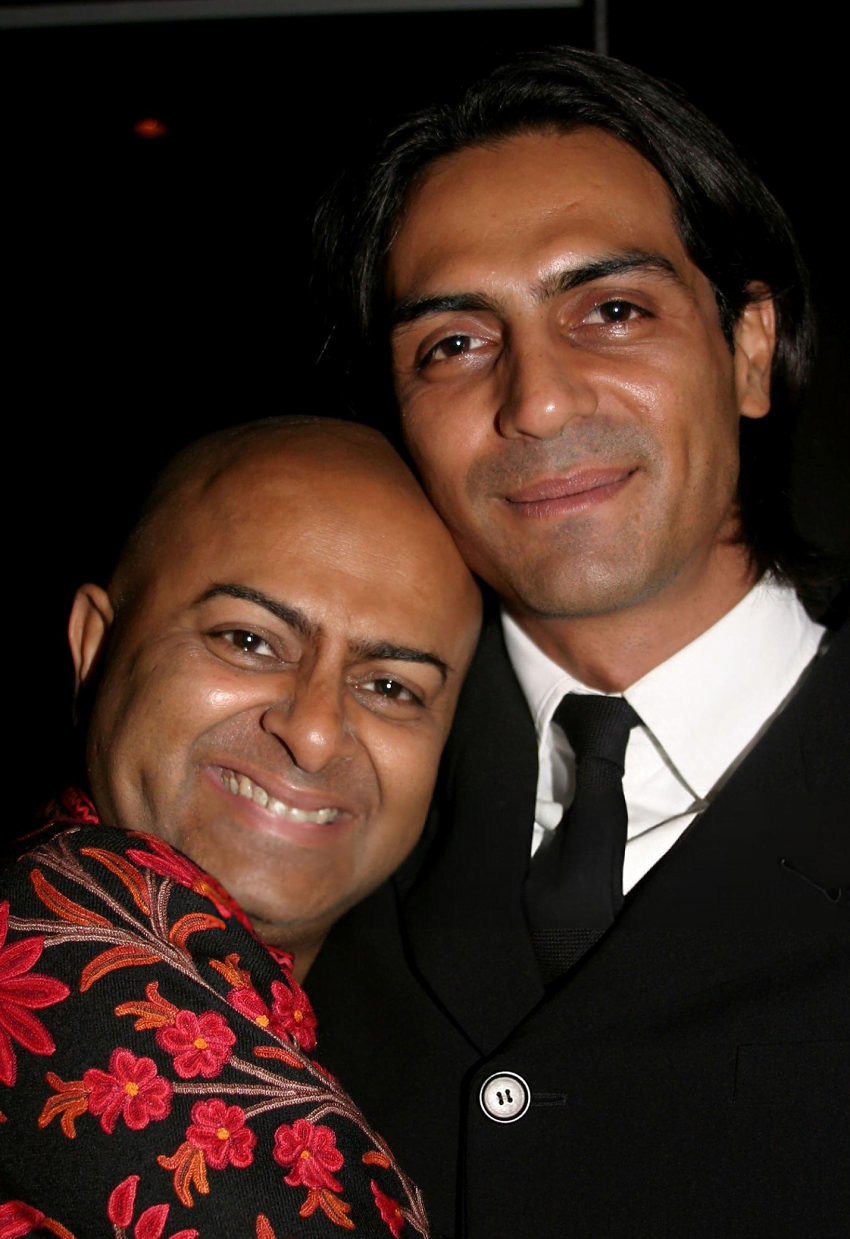
অর্জুন রামপালের সঙ্গে
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা সামাজিক বিদ্রোহ ছিল ‘চোখের বালি’ উপন্যাস। সেই উপন্যাস নিয়ে প্রথম ছবি হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকতে, ১৯৩৮ সালে। পরিচালক ছিলেন সতু সেন। সঙ্গীত পরিচালক অনাদি দস্তিদার। অভিনয়ে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, ছবি বিশ্বাস, হরেন মুখোপাধ্যায়, সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়, ইন্দিরা রায়, শান্তিলতা ঘোষ ও রমা বন্দ্যোপাধ্যায়।
দ্বিতীয় ‘চোখের বালি’ ২০০৩ সালে। পরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষ। অভিনয়ে ঐশ্বর্য রাই বচ্চন, রাইমা সেন, লিলি চক্রবর্তী, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় ও টোটা রায়চৌধুরী। প্রপস এল সঞ্জয় লীলা বনশালির ‘দেবদাস’-এর গোডাউন থেকে। ঐশ্বর্যের জন্য সাহারা ইন্ডিয়ার তরফ থেকে এক লরি কালো পোশাকের সিকিওরিটি এল। সে এক ধুন্দুমার কাণ্ড!
ভারতে চলচ্চিত্রের জন্য জাতীয় পুরস্কার শুরু হয় ১৯৫৪ সাল। সুতরাং ১৯৩৮-এর প্রথম ‘চোখের বালি’র প্রশ্ন নেই। দ্বিতীয় ‘চোখের বালি’ জাতীয় পুরস্কার পেল। সামগ্রিক ছবির বিচারে বাংলার সেরা ফিচার ফিল্ম, সেরা কস্টিউম ডিজ়াইনের জন্য জাতীয় পুরষ্কার। শ্রেষ্ঠ শিল্প নির্দেশনার জন্য জাতীয় পুরষ্কার। ব্যবসা করল ভাল। প্রযোজক সংস্থা এই ছবির হাত ধরে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করল। গোটা দেশে পরিচিত হল। অনেক প্রাপ্তি ছিল এই ছবি ঘিরে। তবু কী যেন একটা কম ছিল! গ্ল্যামারের আড়ালে যা চাপা পড়ে গিয়েছিল।
আরও পড়ুন: ‘এতগুলো মালয়ালম ছবি করার পর ভাষাটা রপ্ত হয়ে গিয়েছে’
অপ্রাসঙ্গিক যদিও, তবু একটা ছোট্ট গল্প বলি। শুধু জানাবার জন্য। এই ছবির কাস্টিং নিয়ে বহু শোরগোল হয়েছিল। যাইহোক, শেষ পর্যন্ত ঐশ্বর্য হলেন বিনোদিনী আর আশালতা সাজলেন রাইমা সেন। রাইমাকে সেকেলে লুকে এত মানিয়েছিল যে অভিনয়ের ঘাটতিটা পুষিয়ে গিয়েছিল। রাইমাকে নেওয়ার পিছনে ঋতুপর্ণর একটা অন্য উদ্দেশ্য ছিল। যেটা প্রথমদিকে কেউ বুঝতে পারেনি। শুটিংয়ের আগে ঋতু মাঝেমাঝেই রাইমাকে ডেকে শাড়ি পরিয়ে ছবি তুলতেন। ছবির ব্রোমাইড হাতে দিয়ে বলতেন, ‘ছবিগুলো তোর দিদিমাকে দেখাস তো ডলু। শাড়ি পরাটা ঠিক হচ্ছে কিনা জিজ্ঞাসা করিস। উনি তো ‘দেবী চৌধুরানী’ করেছেন!’ রাইমার দিক থেকে খুব একটা উৎসাহ দেখতেন না ঋতু। বাধ্য হয়ে একদিন বলেই ফেললেন, ‘তোর দিদিমার সঙ্গে শাড়ি নিয়ে একটু আলোচনা করতে ইচ্ছে করে। তখনকার দিনে কীরকমভাবে শাড়ি…মানে বলতে চাইছি শাড়ি পরার কায়দা…আসলে ‘চোখের বালি’ তো…’
রাইমা ইংরেজিতে যা বলেছিল তার মানে নাকি দাঁড়ায়, সে গুড়ে বালি। রাইমার দিদিমা সুচিত্রা সেনকে আর দেখা হল না ঋতুপর্ণর। একটা আক্ষেপ থেকেই গেল।

‘চোখের বালি’ ছবিতে টোটা ও ঐশ্বর্য
জীবনের শেষ অধ্যায়টা ঋতুপর্ণর শরীরসত্তার চরম বিকাশ ঘটেছিল। ট্রান্সওমেন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। তাতে ধুনো দিয়েছিলেন সহযোগীরা। বা আটকানোর উপায় ছিল না বলা যেতে পারে। ফলে, ছবিগুলো একান্ত ব্যক্তিগত চাহিদার হয়ে গেল। সর্বজনগ্রাহ্য হল না। তাতে অসুবিধে নেই। সব সিনেমা সবাই দেখেন না। সত্যজিৎ থেকে শুরু করে বিশ্বের ঘিলু নাড়িয়ে দেওয়া পরিচালকদের ছবি সুপারহিট হয়নি। মাথাটাকে শুধু ঘুরিয়ে দিয়েছে। ভাবনা, বিষয় বৈচিত্রে ঋতুপর্ণর ‘চিত্রাঙ্গদা’ সেই রাস্তাতেই হেঁটেছে। কিন্তু তত্ত্বটাকে খাড়া করার জন্য এতবার কলম বোলানো হয়েছে যে, কখনও-কখনও ক্লান্ত লেগেছে।
ফিল্ম জগতে একটা লিখিত সূত্র আছে। ‘অ্যা ডিরেক্টর ইজ় অ্যাজ় গুড অর অ্যাজ় ব্যাড অ্যাজ় হিজ় লাস্ট ফিল্ম।’ তরুণ মজুমদার এই বাক্যটি খুব বিশ্বাস করতেন। বলতেনও। যদিও তাঁর নিজের জীবনে এই প্রশ্নেরই সম্মুখীন হতে হয়েছিল। অতীতে তুমি যাই করো না কেন, পরিচালক হিসেবে তোমার মূল্য নির্ধারণ হবে শেষ ছবিতে তুমি কেমন করলে, তার ওপর।
কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালিত, ঋতুপর্ণ অভিনীত ‘আর একটি প্রেমের গল্প’। ঋতুপর্ণ পরিচালিত ও অভিনীত ‘চিত্রাঙ্গদা’। এই দুটি ছবি ঋতুপর্ণকে অনেক প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। শেষ ছবি ‘সত্যান্বেষী’, শেষ তথ্যচিত্র তাঁর প্রিয়তম মানুষ, যাঁকে আঁকড়ে ছিলেন আবাল্য, সেই রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে করলেন, ‘জীবনস্মৃতি’। যে অসম্পূর্ণ জীবনস্মৃতি মাত্র পঞ্চাশ বছর বয়সে লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। শেষ দুটি কাজ ঋতুপর্ণর একুশ বছরের ফিল্মি জীবনে একটি বিরাট বিস্ময় চিহ্ন দেগে দিয়েছিল।
আরও পড়ুন: জাতীয় সঙ্কটে বাংলা ছবি, উদ্বিগ্ন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্যরা
শেষ ছবির মূল্যায়নই যদি প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব হয়, তাহলে তো কথা উঠতেই পারে! ঋতুপর্ণ ঘোষের শেষটা ঠিক শেষ হয়নি। হয়তো আরও কিছু দেওয়ার ছিল। আরও কিছু বলার ছিল! ঈশ্বর বিশ্বাস করতেন না ঋতুপর্ণ। তবে হাত দিয়েছিলেন রাধাকৃষ্ণর চিত্রনাট্যে। আর একটি প্রেমের কাহিনি। একটি মধুর বিরহের গল্প! ঋতুপর্ণ সারাজীবন ভালবাসা খুঁজে বেরিয়েছিলেন পাগলের মতো। প্রেম এসেছিল হয়তো, শুধু সুখ চলে গিয়েছিল। চরম এক আক্ষেপের অসুখ আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ধরেছিল ওঁকে। যার নাগপাশ কেটে বেরোনোর জন্য ছটফট করেছিলেন শেষ দিনগুলোয়।
জীবনের শেষ ছবি, ‘আগন্তুক’ মুক্তি পেয়েছে। প্রশংসা হচ্ছে। সত্যজিৎ রায় এক রাত্রে বিজয়া রায়কে বলেছিলেন, ‘সিনেমায় আমার যা কিছু বলার ছিল সব শেষ হয়ে গেল।’
ঋতুপর্ণও এক অসমাপ্ত জীবনস্মৃতি এঁকে গেলেন। ঠিক পঞ্চাশ বছর বয়সেই। প্রশ্নগুলো তবু থেকেই গেল।
ছবি: গেটি ইমেজেস
Edited and Published by Prabuddha Neogi
আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল ফলো করুন