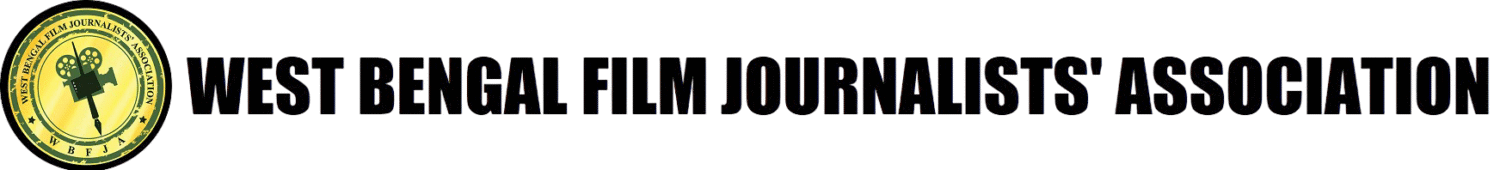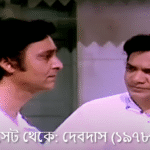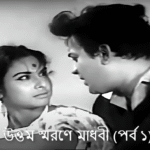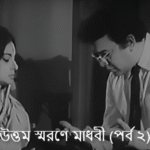ট্রিলজির শিরোপা দিতে এত কার্পণ্য কেন?
তেতাল্লিশের মন্বন্তরকালে পাড়ায় অভুক্তদের খাওয়াতে গণ-রান্নাঘর খুলেছিলেন যুবক উত্তমকুমার ও তাঁর বন্ধুরা। কোভিডকাল যেন ফিরিয়ে এনেছিল সেই সময়। ‘সদানন্দের মেলা’তেও ছিল কমিউনিটি কিচেন, অতিমারীর সময় মনে করিয়ে দিয়েছিলেন সম্রাট মুখোপাধ্যায়। WBFJA-এর পাতায় রইল সেই লেখার পুনর্মুদ্রণ
১
একটি বাড়ি। আর মাথার ওপরে ছাদ হারাতে চলা একঝাঁক মানুষ। আর একজন যুবক। সেও ওই পরিযায়ী-বাস্তুচ্যুত মানুষদেরই অংশ। কখনও তার নাম চঞ্চল। কখনও অজিত। আবার কখনও প্রতাপ। তিনটি চরিত্র। তিনটি ছবিতে। ছবি তিনটি হল ‘ওরা থাকে ওধারে’ (Ora Thake Odhare), ‘সদানন্দের মেলা’ (Sadanander Mela) আর ‘হাত বাড়ালেই বন্ধু’ (Hath Baralei Bondhu)। একটি সুতোয় তিনটি ছবি গাঁথা। সবক’টিতেই নায়ক চরিত্রে উত্তমকুমার। আরেকটি সূত্রও আছে। তিনটিরই কাহিনিকার, চিত্রনাট্যকার এবং গীতিকার সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র। সঙ্গে সবক’টি ছবিরই পরিচালক সুকুমার দাশগুপ্ত।
একই পরিচালক। একই চিত্রনাট্যকার। একই নায়ক। চিত্রনাট্যের কেন্দ্রবিন্দুতে একই সামাজিক সমস্যা। এর পরও যে তিনটি ছবিকে ট্রিলজির শিরোপা দিতে আমাদের এত কার্পণ্য, তার কারণ হয়তো জনপ্রিয় সিনেমা সম্পর্কে আমাদের সযত্নলালিত উন্নাসিক উপেক্ষা। অথচ এমনতর ‘মুদ্রাদোষ’ না থাকলে, দেখতে পেতাম, এদের অভ্যন্তরে বাঙালির সমাজজীবনের এক ঐতিহাসিক রূপান্তর-পর্ব কেমন ধরা আছে।
২
সময়টা পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে। দেশ সদ্য স্বাধীন। প্রচুর আশা-আকাঙ্ক্ষা সঙ্গে অবসাদও। কারণ, কপালে ভাঁজ ঘনিয়ে আনার মতো উপাদানও যে প্রচুর বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনে। অল্পকাল আগে ঘটে যাওয়া দেশভাগ আর দাঙ্গা তখনও নাগরিক মনে ত্রাসের ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে। ভুলতে চাইলেও ভোলা যায় না, কারণ জীবন্ত স্মারকের মতো নিয়ত শরণার্থীর স্রোত বহমান। দুর্ভিক্ষের স্মৃতি কাটিয়ে উঠেও খাদ্যের অপ্রতুলতা মেটেনি। ‘আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়…’, কিশোর-কবির এই পংক্তি যুদ্ধের দিনগুলো পেরিয়ে এসেও বাস্তব।
তবু খাদ্যের সমস্যাকেও ছাপিয়ে গিয়েছে বাসস্থানের সমস্যা। ‘ঠাঁই নেই, ঠাঁই নেই, ছোট এ তরী।’ মহানগর কলকাতা ক্রমশ আর ‘বাবু’দের বসবাসের শহর নয়। সে শহর তখন ফুটপাথের কুলি-মজুরদের, নবোদ্ভূত শ্রমিকের, রিকশাওয়ালার। তাদের নায়ক করে ছবির ফ্রেমে রূপকথা আঁকছেন চিত্তপ্রসাদ ভট্টাচার্য। গান লিখে সুর করছেন সলিল চৌধুরী। কলমে শব্দ খোদাই করছেন মানিক বাঁড়ুজ্যে, সুভাষ মুখুজ্যেরা। বাস্তব ও শিল্প, দু’দিকের চাপে বাঙালি মধ্যবিত্তের জন্য তখন কোনও গরিমা আর পড়ে নেই। প্রলেতারিয়েত হিরো সে হতে পারবে না। অতখানি শ্রেণীচ্যুতি তার ধাতে সইবে না। বা সব চক্ষুলজ্জা ছেড়ে সে দাঁড়াতে পারবে না সাহায্যপ্রার্থীর লাইনে। আবার অফিসবাবুর নিস্তরঙ্গ, আলস্যময় জীবন যে ভোগ করে এসেছে এতদিন এই মহানগরে, তাও যেন তখন দূরের নীহারিকা!
আরও পড়ুন: ‘এখনকার ছবি শুক্রবারে আবিষ্কার, সোমবারে পরিষ্কার’
তার সামনে তখন অফিস মানে কেবলই চাকরি যাওয়ার ভয়। দেশভাগ হঠাৎই শ্রমের বাজারে বেকারের জোগান অঢেল বাড়িয়ে দিয়েছে যে! পাশে আর এক ভয়, পুরনো ভাড়াবাড়ি হারানোর। ‘ভাড়াটে’ শব্দটার এই সময় থেকেই ‘নিম্নবর্গ’ হয়ে পড়া। তখনও অফিসযাত্রী বাঙালির বৃত্তান্ত এতটা মফসসলি নয় যে।
এই সংকটকালে বাংলা সিনেমাতেই একমাত্র তখনও মধ্যবিত্ত নায়ককে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল। ফলে সেখানে দরকার ছিল নিষ্পাপ এক যুবক-মুখের উত্থান, যে মুখ এই দশকের শোককে ধারণ করতে পারবে। আবার সেই মুখ প্রয়োজনীয় দৃঢ়তায় এই সমস্যা থেকে আত্মপ্রতিষ্ঠায় উঠে আসার রূপকথাকেও ধারণ করতে পারবে। প্রমথেশ বড়ুয়ার সাহেবি ধাঁচের রাজকুমার-সুলভ প্রচ্ছদপট এ কাজের ভার-বহনে সক্ষম ছিল না। বরং এ শহরেরই এক মধ্যবিত্ত ঘর থেকে উঠে আসা শ্রীমান অরুণের সাদামাটা বিশেষত্বহীন মুখে এই শোক আর স্বপ্নের চিহ্নগুলো সহজে বাংলা সিনেমা মুদ্রিত করে দিতে পেরেছিল।
আরও পড়ুন: ‘এক ফিল্ম হিরোর কাছ থেকে প্রেমের প্রস্তাব পেয়েছি’
সেই পথে ‘ওরা থাকে ওধারে’, ‘সদানন্দের মেলা’ আর ‘হাত বাড়ালেই বন্ধু’ এই তিন ‘কমেডি’ ছিল সিঁড়ির তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। জনগণমনের নায়ক হয়ে ওঠার পথে।
সমাজতত্ত্ববিদ ম্যাক্স হেব্বার একবার বলেছিলেন, একজন তারকার দ্যুতি হয়তো সাময়িক, কিন্তু তাঁকে ঘিরে তৈরি আখ্যানের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। এটাই জনপ্রিয় সংস্কৃতির নিয়ম ও ক্ষমতা। সত্যিই এই ২০২১-এ পৌঁছে যখন এই ছবিগুলো দেখি, কী যে চেনা লাগে! ক্ষতে ও উপশমে। বুঝি যে ‘আলো ক্রমে আসিতেছে’। আজও।
৩
‘ওরা থাকে ওধারে’ ছবিতে এক ভাঙাচোরা বাড়িতে ভাড়াটে দুই পরিবারের এক পক্ষ ঘটি, অন্যপক্ষ বাঙাল। কেউই নিজের অতীত আত্মগরিমা প্রচারে কম যায় না। এদের লড়াইও যত, ভালোবাসাও তত। তাই একটি পরিবার যখন কাবুলিওয়ালার তাগাদার চাপে রাতের বেলায় গোপনে বাড়ি ছাড়তে চলে, তখন অন্য পরিবার তাদের বাঁচায়। মধুরেণ সমাপয়েতে বাঙাল ঘরের সুচিত্রা সেনের সঙ্গে বিয়ে হয় ঘটি উত্তমকুমারের। তারা দু’জনে এগিয়ে যায় বাঙালির আসন্ন মিলিত ইতিহাসের দিকে। পঞ্চাশের দশকের মধ্যভাগে এমন নতুন বাঙালি সমাজ যখন গড়ে উঠছে, ঠিক তখনই এ ছবি যেন বলতে চেয়েছে, আপাতত বেড়ার এপারের ওপারের তুচ্ছ আচার-বিচারের দ্বন্দ্ব ভুলে একে অপরের পাশে না দাঁড়াতে পারলে বাঙালির সামনে ভারী দুর্দিন।
মনে পড়ে, এই তো সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারকালেই দেখেছি বাঙালির এই দুই ভূখণ্ডে ভাগ হয়ে থাকার বিষয়টি নিয়ে এক বিশেষ ‘বহিরাগত’ রাজনৈতিক পক্ষের কী চেষ্টা, বিভাজনের বিষ ঢালার! আমাদের গেরস্থালির মজাদার ঘটি-বাঙাল-খুনসুটিকেও রাজনৈতিক তাস হিসাবে ব্যবহার করবার সে কী মর্মান্তিক চেষ্টা! কিন্তু সে মরণপণ চেষ্টার পরিণতিতে এরা যে সফল হল না, বরং মিলল প্রবল এক চপেটাঘাত, তা হয়তো এই ‘ওরা থাকে ওধারে’র মতো ছবি আজও বাঙালির শিকড়ে থাকে বলে। বুঝতে পারি, সে আমলে উত্তম-সুচিত্রার রূপকে বাঙালি দর্শক আসলে দুই বাংলার দুই প্রতিনিধির (মজার কথা, ব্যক্তিগত জীবনেও সুচিত্রা পূর্ববঙ্গীয় আর উত্তম প্রবল ক্যালকাটান) পারিবারিক মিলন দেখতে চাইছিল বারবার (‘সবার উপরে’ বা ‘বিপাশা’ও প্রাসঙ্গিক)। এইসব ছবি এতটাই ইতিহাসের জলহাওয়া মাখা। আর এইসব ছবি এতটাই বর্তমানের মাটিতে দাঁড়িয়ে।
আরও পড়ুন: ‘এতগুলো মালয়ালম ছবি করার পর ভাষাটা রপ্ত হয়ে গিয়েছে’
‘সদানন্দের মেলা’তেও বাস্তুচ্যুত গরিব মানুষদের কাহিনি। এক ধনী শিল্পপতির মেলা বাড়ি ফাঁকা পড়ে থাকে শহরে। ওদিকে একদল ঘরবাড়িহীন মানুষ আস্তানার খোঁজে পথে-পথে ঘুরে বেড়ায়। আর্থিক মন্দায় তাদের চাকরি গিয়েছে বা যায়-যায়। কিছু মজাদার চালাকির আশ্রয় নিয়ে এমনই একখানা ফাঁকা বাড়ি দখল করে এইসব মানুষদের ঠাঁই দেন ভবঘুরে শিল্পী সদানন্দ (ছবি বিশ্বাস)। তাঁর চরিত্রটি চ্যাপলিনের হৃদয়বান ট্র্যাম্পের কথা মনে করায়, যে মজার ছলে নগ্ন করে দেয় ধনবাদী সভ্যতার অমানবিক চেহারাকে। এই বাড়ি দখলে দোসর হয় অজিত (উত্তম) আর শীলা (সুচিত্রা)। এ ছবি বারবার বলে, যার প্রচুর আছে, সময় এসেছে তার এবার খানিকটা ভাগ দেওয়ার। কেড়ে নেওয়ার গল্প একরকম। এই ছবি অতটা কড়া হয় না। বরং বাণিজ্যিক ছবির কোডগুলো মেনে মজার চলে দেখায়, কেমনভাবে ধনী মালিককেও এনে দাঁড় করানো যায় অসহায় সর্বস্বহারা মানুষদের লাইনে। এর ছ’বছর পরে প্রথমবারের খাদ্য আন্দোলনের পরের বছরে প্রেমেন্দ্র-সুকুমাররা ভাড়াটে জীবনের যন্ত্রণা নিয়ে আরেকবার মজার ছলে করেন যে ‘হাত বাড়ালেই বন্ধু’ (এবার নায়িকা সাবিত্রী), তাও ওই একই কথা বলতে।
আরও পড়ুন: অবশেষে মুক্তি পেতে চলেছে ‘সেলাই’
আজ যখন এসব ছবি আমরা দেখতে বসি, তখন দুনিয়াজোড়া এক সংকটকালে আবার পাড়ায় পাড়ায় যৌথ রান্নাঘর, সস্তার রান্নাঘর এইসব খুলছে। দুর্ভিক্ষ নয়, মহামারি যার কারণ। আবার বহু মানুষ চাকরিচ্যুত। পথে পরিযায়ী শ্রমিকের স্রোত। ধনবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আরও নির্মম। এত নিষ্ঠুরতা, এত কান্নার পাশে এটাও দেখি মানুষ হাল ছাড়ছে না। আর মানুষই মানুষের হাত ধরছে। এই ট্রিলজিকে তখন আর নিছক ভিন্টেজ বিনোদন বলে মনে হয় না। মনে পড়ে চার্লস স্পেনসর চ্যাপলিন বলেছিলেন, ট্র্যাজেডি হলো লং শট কিন্তু কমেডিই হলো কাছের ক্লোজ়আপ।
‘সদানন্দের মেলা’র এক দৃশ্যে দেখি আশ্রিতের দল বসে হিসেব করছে একসঙ্গে খাবার ব্যবস্থা চালু রাখতে মাসে-মাসে কে কতটা কী দিতে পারবে। কমিউন গড়তে হবে যে। মনে পড়ে, তরুণকুমারের স্মৃতিকথায় পড়েছি, তেতাল্লিশের মন্বন্তরকালে পাড়ায় অভুক্তদের খাওয়াতে কেমন গণ-রান্নাঘর খুলেছিল যুবক উত্তম ও তাঁর বন্ধুরা। রোজ পাঁচ-ছ’হাজার মানুষের পাত পড়ত সেখানে! আবার আজও যেমন পাড়ায়-পাড়ায় দেখি একদল যুবক দিনের পর দিন টেনে নিয়ে যাচ্ছে এইরকম সব রান্নাঘর। শুধু নিজের নয়, অন্যের খাওয়ার হিসেবও নিচ্ছে তাঁরা। তখন বাঙালি জীবনের ইতিহাসের ইতিবাচক দুই প্রান্তকে জুড়ে যেতে দেখি।
আর তখনই উত্তমকুমার আর দূরের তারকা থাকেন না। এইসব চেনা ছেলেদেরই কারও মুখচ্ছবি ফুটে ওঠে তাঁর মুখে।
এই উত্তমকে অতীত-নক্ষত্র বলবে কে?
প্রথম প্রকাশ: আজকাল, জুলাই ২০২১
Edited by Kamalendu Sarkar
Published by Prabuddha Neogi
আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল ফলো করুন